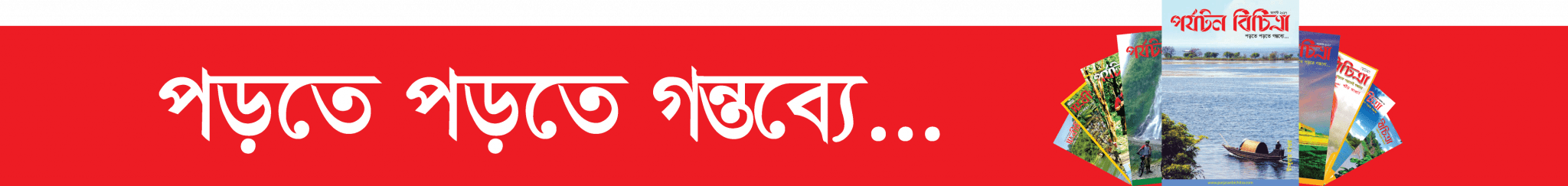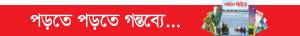পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক
বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এক ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদ গড়ে উঠেছিল এই বগুড়ায়। প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়, যা বগুড়া জেলায় অবস্থিত। বগুড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বারও বলা হয়ে থাকে একে। বগুড়া শুধু দইয়ের জন্যই বিখ্যাত না, অনেক দর্শনীয় স্থানও আছে এখানে। চলুন জেনে নেয় এই জেলার উল্লেখযোগ্য ১১ গন্তব্য সম্পর্কে।
মহাস্থানগড়
মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। বগুড়া জেলাশহর থেকে ১৩ কিমি. উত্তরে শিবগঞ্জ উপজেলায় করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থান ছিল এই মহাস্থানগড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে পুণ্ড্র নামে একটি অনার্য সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল।
তৎকালীন সমগ্র বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন এ দুর্গনগরী পর্যায়ক্রমে মাটি ও ইটের বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত যা উত্তর-দক্ষিণে ১৫২৫ মিটার (৫০০০ ফুট) দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৭০ মিটার (৪৫০০ ফুট) প্রশস্ত এবং চতুর্পার্শ্বস্থ সমতলভূমি থেকে ৫ মিটার (১৬ ফুট) এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৬ মিটার (১২৮ ফুট) উচু।
বেষ্টনী প্রাচীর ছাড়াও পূর্বদিকে নদী ও অপর তিনদিকে গভীর পরিখা নগরীর অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এই দুর্গের আয়তন প্রায় ১৮৫ হেক্টর। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান পরাক্রমশালী মৌর্য, গুপ্ত এবং পাল শাসকবর্গের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে হিন্দু সামন্তরাজাদের রাজধানী ছিল।
দুর্গের বাইরে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ৭/৮ কিলোমিটারের মধ্যে এখনও বিভিন্ন ধরনের বহু প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে, যা উপশহরের সাক্ষ্য বহন করে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে (৬৩৯-৬৪৫) পুণ্ড্রনগর পরিদর্শনে এসেছিলেন। তার ভ্রমণ বিবরণীতে এখানকার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮০৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন মহাস্থানগড়ের অবস্থান প্রথম চিহ্নিত করেন।
তারপর প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষকে হিউয়েন সাঙ বর্ণিত পুণ্ড্রনগর হিসেবে শনাক্ত করেন। ১৯২৮-১৯২৯ সালে মহাস্থানগড়ে সর্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু করা হয়। এসময় নগরীর মধ্যে বৈরাগীর ভিটা, মুনির ঘোন ও বাইরে গোবিন্দ ভিটা নামক ৩টি স্থানে খনন হয়। দীর্ঘদিন পর ১৯৬০-১৯৬১ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৮৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে দুর্গের বিভিন্ন অংশ খনন করা হয়।
১৯৯৩ থেকে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স সরকার যৌথভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক অনুসন্ধান ও খননের ফলে দুর্গ নগরীর অভ্যন্তরে চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে মুসলিম যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৮টি স্তরে প্রাক মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও মুসলিম যুগের কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি, রাস্তা, নর্দমা, নালাকূপ, মন্দির, মসজিদ, তোরণ, বুরুজ ইত্যাদি উন্মোচিত হয়েছে।
এসব স্থাপত্য কাঠামো ছাড়াও মৌর্য যুগের টাপিযুক্ত শিলা খণ্ড, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা ও ছাঁচে ঢালা তাম্র মুদ্রা, কালো মসৃণ মৃৎ পাত্র, পোড়ামাটির ফলক, প্রস্তর ও পোড়ামাটির মূর্তি, স্বল্প মূল্যবান প্রস্তর, জালের কাঠি এবং মাটি ও ধাতব দ্রব্যাদি, প্রচুর সাধারণ মৃৎপাত্র এবং আরবি উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একটি প্রস্তর ফলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
ভাসু বিহার
ভাসু বিহার বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন প্রত্ননিদর্শন। এটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়, মহাস্থানগড় থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে বিহার ইউনিয়নের বিহার নামক গ্রামে অবস্থিত। আলেকজান্ডার কানিংহাম ভাসু বিহার এবং সাত শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং উল্লিখিত পো-সি-পো বিহার অভিন্ন মনে করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে নরপতির ধাপ নামে পরিচিত ভাসু বিহারটির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয় প্রথমবারের মতো। এর ফলে পরবর্তী গুপ্তযুগের দুটি আয়তক্ষেত্রাকার বৌদ্ধ বিহার এবং একটি প্রায় ক্রুশাকৃতি মন্দির উন্মোচিত হয়েছে।
প্রথম বিহার উত্তর-দক্ষিণে ১৪৮.১৩ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৯ মিটার পরিমাপের প্রায় আয়তক্ষেত্রাকার বিহারটি পোড়া ইটের তৈরি। দুই ইটের মাঝখানে মর্টার হিসেবে কাদামাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। ভূমি পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বিহারটি প্রথম বিহারের প্রায় অনুরূপ এবং উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। উন্মুক্ত আঙিনার চারদিকের বারান্দাসংলগ্ন প্রথম বিহারে ২৬টি এবং দ্বিতীয় বিহারের ৩০টি কক্ষ আছে। প্রধান মন্দিরটি ছিল কমপ্লেক্সের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে, ২ নম্বর বিহারের দক্ষিণে এবং ১ নম্বর বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে। মন্দিরটিতে ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ির প্রদক্ষিণ পথ আছে।
প্রত্নতাত্ত্বিক উত্খননের ফলে বিহার এবং মন্দির স্থাপত্যের ভিত্তি ছাড়াও ব্রোঞ্জমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, অক্ষর খোদিত পোড়ামাটির সিল, অলংকৃত ইট এবং মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। কক্ষগুলোর অভ্যন্তর থেকে ৬০টিরও বেশি ব্রোঞ্জমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, মূর্তিগুলোর কিছু হয়তো বিহার নির্মাণ যুগের আগেই তৈরি এবং পরবর্তীকালে সেগুলো বিহারে রাখা হয়েছিল। সব মূর্তির পেছনে স্লাব ও উঁচু পেডেস্টাল ছিল। মূর্তিগুলোর মধ্যে বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং বোধিশক্তি উল্লেখযোগ্য।
ভাসু বিহারে প্রাপ্ত মূর্তির দীর্ঘ হালকা-পাতলা শরীর, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বুক এবং মার্জিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পালযুগের ধ্রুপদি শিল্পকলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ময়নামতির খাটো এবং মোটা, সরল এবং স্থূল প্রকৃতির মূর্তি থেকে ভাসু বিহারের নিদর্শনগুলো ভিন্নরূপের। এ ছাড়া ২৫০টির বেশি অক্ষর খোদিত সিল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১০০টির বেশির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। মানুষ, পাখি, বিভিন্ন প্রাণী, ফুল, লতাপাতা এবং জ্যামিতিক নকশা ছিল পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু। পাহাড়পুর, ময়নামতিসহ অন্যান্য বৌদ্ধ স্থাপত্যের মতো ভাসু বিহারে ইট অলংকরণে পদ্মের পাপড়ি এবং ধাপ-পিরামিড বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।
মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর
মহাস্থানগড়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৬৭ সালে করতোয়া নদীতীরে মহাস্থানগড়ের টিলা সংলগ্ন এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে মহাস্থানগড় ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করা প্রাচীন সামগ্রী পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণ করা হয়। কয়েক হাজার বছর আগের সোনা, রুপা, লোহা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঁসাসহ বিভিন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থ ও পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি, আত্মরক্ষার জন্য ধারালো অস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।
মহাস্থানগড় জাদুঘর প্রাঙ্গণে ফুলবাগান তৈরি করে চারপাশে নানা জাতের গাছ লাগিয়ে এর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহাস্থানগড়ের টিলাসংলগ্ন আমবাগানে গড়ে তোলা হয়েছে পিকনিক স্পট। এছাড়াও দেশ-বিদেশের অতিথিদের জন্য করতোয়া নদীর পাড়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
মাহিসওয়ার (র.)-এর মাজার
বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এই মাজার অবস্থিত। শাহ সুলতান বলখী ১৪শ শতাব্দীর একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান বগুড়া জেলা) ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শাহ সুলতান মধ্য এশিয়ার বলখ রাজ্যের সম্রাট শাহ আলী আসগরের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজসিংহাসন ছেড়ে সিরিয়ার দামেস্ক এসে শেখ তৌফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পীরের নির্দেশে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে বাংলার সন্দ্বীপে আসেন। পরে তিনি মহাস্থানগড়ে (পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী) এসে স্থায়ী হন।
ঐতিহাসিক সূত্রমতে, সুলতান বলখী ১৩৪৩ খ্রিষ্টব্দে পুণ্ড্রবর্ধনের শেষ রাজা পরশুরামকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, শাহ সুলতান (র.) তার শিষ্যদের নিয়ে ফকিরবেশে একটি মাছ আকৃতির নৌকাতে করে ভিন্নমতে, মাছের পিঠে আসীন হয়ে মহাস্থানগড় এসেছিলেন। সেখান থেকে তার নামের সাথে যুক্ত হয়েছে মাহিসওয়ার (মাছের পিঠের আরোহী) এবং তিনি বলখ থেকে এসেছিলেন বলে তাকে শাহ সুলতান বলখী বলা হয়।
মহাস্থানগড় পৌঁছে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এতে প্রথমে রাজা পরশুরামের সেনাপ্রধান, মন্ত্রী এবং কিছু সাধারণ মানুষ ইসলামের বার্তা গ্রহণ করে মুসলমান হয়। এভাবে পুণ্ড্রবর্ধনের মানুষ হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলে স্থানীয় রাজা পরশুরাম শাহ সুলতানকে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়। ফলে বলখীর সাথে রাজার বিরোধের এক পর্যায়ে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে রাজা পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। এখানে সমাহিত শাহ সুলতান বলখীর মাজারে প্রতিদিন বহু লোকের সমাগম ঘটে।
বাবা আদমের মাজার ও আদমদিঘি
বগুড়া শহর থেকে ৩৫ কিমি. দূরে আদমদিঘি সদর ইউনিয়নে বাবা আদমের মাজার ও দিঘি অবস্থিত। ১৩শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের এ অঞ্চল শাসন করতেন রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন। তার রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর। তার শাসন আমলে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা নির্যাতিত হতো। ওই সময় আরাকান রাজ্য থেকে হজরত বাবা আদম (র.) নামে এক গুলি তার ১২ জন শিষ্য নিয়ে এই এলাকায় এসে আস্তানা গড়ে তোলেন।
তার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাহ তারকান, শির মোকাম, শাহ্ বন্দেগী, শাহ জালাল, শাহ ফরমান ও শাহ আরেফিন। বাবা আদম (র.) এবং তার শিষ্যদের ব্যবহার ও আচরণের কারণে তারা অল্পদিনেই স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সে সময়ের হিন্দুপ্রধান এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে বগুড়া জেলার শেরপুর হয়ে যমুনা নদী পর্যন্ত বাবা আদম (র.)-এর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এ সময় আদমদিঘির জনসাধারণ খাবার পানির সংকটে ভুগছিল। বাবা আদম (র.)-এর আহ্বানে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম এসে এখানে একটি দিঘি খনন করে।
সে সময় এলাকাবাসী বাবা আদম (র.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ স্থানটির নামকরণ করে আদমদিঘি। পরবর্তীতে রাজা বল্লাল সেনের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে বাবা আদম (র.) আহত হন। আহত অবস্থায় তাকে আদমদিঘিতে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। তার অছিয়ত মতে দিঘির দক্ষিণ পাড়ে তাকে কবর দেওয়া হয়। সেই থেকে এটি আদম বাবার মাজার নামে পরিচিতি পায়।
খেরুয়া মসজিদ
শেরপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে খেরুয়া মসজিদের অবস্থান। মসজিদে স্থাপিত একটি লিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি ৯৮৯ হিজরিতে (১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ) জওহর আলী খান কাকশালের পুত্র নবাব মির্জা মুরাদ খান নির্মাণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ষোলো শতকের শেষার্ধে এ অঞ্চলে কাকশাল গোষ্ঠী দ্বারা একটি মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি (শেরপুর মোর্চা নামে ইতিহাসে লিখিত) কাকশালদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। পরবর্তীতে তারা মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
খেরুয়া মসজিদ বাংলায় বিদ্যমান মোগল শাসনামলের মসজিদসমূহের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত। প্রকৃতপক্ষে মসজিদটি সুলতানি আমলের শেষে, বাংলায় মোগল শাসনের সূচনালগ্নে বারো ভূঁইয়া এবং বাংলায় অবস্থানরত আফগান প্রধানদের মোগল বিরোধী বিদ্রোহ চলাকালে নির্মিত। আয়তাকার মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ১৭.৩৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭.৫ মিটার। মসজিদের ভেতরের মাপ ১৩.৭২ মিটার x ৩.৮ মিটার (৪৫ ফুট × ১২.৫ ফুট)। চারদিকের দেয়াল প্রায় ১.৮৩ মিটার (৬ ফুট) পুরু। মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি অষ্টভুজ মিনার। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে প্রবেশের জন্য তিনটি দরজা এবং মাঝের দরজাটি অপর দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের।
উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও রয়েছে একটি করে দরজা। ভেতরের পশ্চিম দেয়ালে আছে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে তিনটি অর্ধগোলাকার অবতল মেহরাব। মাঝের মেহরাবটি অপর দুটি থেকে আকারে বড়। এই মসজিদটির গম্বুজের সাথে সুলতানি আমলের গম্বুজ নির্মাণশৈলীর মিল রয়েছে। ছাদের কার্নিশের দু’ধার সামান্য বাঁকানো। বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত এমন ছাদ পনেরো শতকে নির্মিত বাংলার অধিকাংশ স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়।
মসজিদের সামনের দেয়ালে প্যানেলিং-এর কাজ করা। এ ধরনের কাজ ঢাকায় অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদেও লক্ষ করা যায়। বাংলার মোগল পর্বের সূচনাকালের মসজিদ হিসেবে খেরুয়া মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মসজিদটি তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাক্ষ্য বহন করে।
বগুড়ার নবাববাড়ি
বগুড়ার নবাববাড়ি সড়কে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক বাড়িটি বর্তমানে ‘দি প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’ নামে পরিচিত। ২০১৬ সালের মে মাসে এটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা করে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। এটি প্রায় ১৮০ বছরের পুরনো দেশের একমাত্র সুসজ্জিত রাজবাড়ি। এই বাড়িটি বাংলার প্রভাবশালী নবাবদের একটি আবাসস্থল- যাদের মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী অন্যতম।
সিঁড়ি বেয়ে প্রথম ও প্রধান কক্ষে ঢুকতেই চোখে পড়ে শিল্পীর আঁকা নওয়াব পরিবারের সদস্যদের ছবি। অন্দরমহলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করা যায় খাজাঞ্চিখানায়। প্রধান কক্ষের বাঁদিকে দুটি কক্ষ রয়েছে- যার একটিতে নবাব পুত্ররা খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করতেন, অন্যটি খাবার ঘর যেখানে সাজানো রয়েছে পুরনো অনেক সামগ্রী। এর পরেই রয়েছে জলসাঘর।
নবাববাড়ির বিভিন্ন কক্ষ ম্যানিকিন দিয়ে সাজানো। সে আমলের পোশাক পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিমার ম্যানকিনগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে- যা দেখলে তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির একটি ধারণা পাওয়া যায়। জাদুঘরের প্রাঙ্গণটি বাগান ও বিনোদন পার্কে রূপান্তর করা হয়েছে- যেখানে শিশুদের বিভিন্ন রাইড রয়েছে। এছাড়াও দর্শনার্থীদের জন্য কুমির, সাপসহ কয়েকটি বন্যপ্রাণী খাঁচাবন্দি করে রাখা হয়েছে। নামমাত্র প্রবেশ মূল্যে এই নবাববাড়িটি যে কেউ ঘুরে আসতে পারেন।
পাঁচপীর মাজার
পাঁচপীর মাজার কাহালু উপজেলার ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিত। পাঁচজন পীর বা ওলি একই স্থানে শায়িত আছেন বলে স্থানটির নামকরণ হয়েছে ‘পাঁচপীর’। মাজারটি উঁচু একটি ঢিবির উপর অবস্থিত। ১৯৫২ সালে এলাকাটি সমতল করার সময় ইট দ্বারা বাঁধানো পাঁচটি কবর আবিষ্কৃত হয়।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল আজিজ (র.) নামের একজন বিশিষ্ট ওলির নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারের জন্য সাত সদস্যের একটি দল প্রথমে এ অঞ্চলে আগমন করেন। পরবর্তীতে নুর উদ্দীন ইয়ামিন (র.)-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আরেকটি দল এখানে আগমন করেন। তারা উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখান থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন।
পরবর্তীকালে পীরগণ মৃত্যুবরণ করলে এলাকার ভক্তগণ পর্যায়ক্রমে তাদের বর্তমান মাজারস্থলে সমাহিত করে। তবে পীরগণের নাম ও তাদের আগমন সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা ও রেল স্টেশন রয়েছে। প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষে এখানে তিন দিনব্যাপী ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মা ভবানীর মন্দির
উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক মা ভবানীর মন্দির। বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে মা ভবানী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটির একদিকে ভবানীপুর বাজার এবং অন্যদিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। আর মন্দিরের চারদিক ঘিরে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে।
কালিকাপুরান অনুসারে, দক্ষযজ্ঞে দেবী সতী স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। সতীর প্রাণহীন দেহ ৫১টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হলে একান্নটি পীঠস্থানের উদ্ভব হয়- যার মধ্যে এটি একটি। প্রাচীন এই মহাতীর্থক্ষেত্রের বর্তমান মন্দির অবকাঠামো নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক দেবোত্তর ১২ বিঘা জমির ওপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।
প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির চত্বরের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণমুখী মূল মন্দির, বামেশ ভৈরব শিবমন্দির, তিনটি শিবমন্দির, ভোগ পাকশালা, নাটমন্দির, দুটি অতিথিশালা, বাসুদেব মন্দির, গোপাল মন্দির, নরনারায়ণ সেবাঙ্গন (শ্যামাপ্রসাদ সেবা অঙ্গন), শাঁখারী পুকুর ও দুটি স্নান ঘাট। বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে তিনটি শিবমন্দির এবং একটি পঞ্চমুণ্ড আসন রয়েছে। নাটোরের রাণী ভবানীর ছোট তরফ এস্টেট এবং অন্যান্য জমিদারদের পক্ষ থেকে এই মন্দিরের অনুকূলে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করা হয়।
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই পীঠস্থান ও তীর্থক্ষেত্রে রামনবমী, শারদীয় দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা, মাঘী পূর্ণিমা, বাসন্তী দুর্গোৎসব, প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ওইসব অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভারত, নেপাল, ভুটানসহ অন্যান্য দেশ থেকেও প্রতি বছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই মন্দিরে সমবেত হন।
তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ বা বিহার
বিহার ধাপ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। স্থানীয়ভাবে এটি তোতারাম পন্ডিতের ধাপ বা তোতারাম পন্ডিতের বাড়ি নামেও পরিচিত। এটি বগুড়ার শিবগঞ্জের বিহার নামক গ্রামে অবস্থিত। এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে নাগর নদী প্রবাহিত হয়েছে। এটি মহাস্থানগড় থেকে প্রায় চার কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ও ভাসু বিহার থেকে প্রায় এক কি.মি. দূরে অবস্থিত।
বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৮-৬৪৫ খ্রি. এই সময়কালে বাংলার এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি মহাস্থানগড় থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে পো-সি-পো বিহার নামে এক বিহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ধারণা করা হয়, এই বিহার ধাপই সেই পো-সি-পো বিহার। এখানে ১৯৭৯-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে খনন কাজ চলে। এতে পশ্চিম অংশে পাশাপাশি দুইটি বৌদ্ধ বিহার এবং পূর্ব দিকে একটি মন্দিরের অবকাঠামো আংশিকভাবে উন্মোচিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫-০৬ সালের দিকে পুনরায় খনন কাজ চালানো হয়। তখন পূর্বে আবিস্কৃত মন্দিরের পাশে আরও একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ উন্মোচিত হয়। দুইটি মন্দিরই উত্তরমুখী।
বিভিন্ন সময়ে খননের ফলে এখানে এক হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রোঞ্জ নির্মিত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, রৌপ্য মুদ্রা, কাঁচের পুঁতি, ৬০টি পোড়ামাটির ফলক চিত্র, পোড়া মাটির সীল মোহর, ধুপদানী, পিরিচ, মাটির পাত্র, ১০০টি নকশা অঙ্কিত ইট, লোহার পেরেক ইত্যাদি।
প্রথম নির্মাণ যুগের স্থাপত্যকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ যুগের কাল নির্ধারণ করা হয় চার অথবা পাঁচ শতক। ধারণা করা হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্মাণকাল ছয় থেকে দশ শতকের। চতুর্থ থেকে পঞ্চম নির্মাণ যুগের স্থাপত্যকর্মে অনেক ক্ষেত্রেই পুরানো ইটের পুনর্ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। আরও ধারণা করা হয় আনুমানিক এগারো থেকে বারো শতক এই সময়ের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এই প্রত্নস্থলটির পতন ঘটে।
যোগীর ভবন
যোগীর ভবন কাহালু উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিমি. উত্তরে পাইকর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। মহাস্থানগড় থেকে এটি ১২ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানটি প্রায় ৮০ একর ভূমিজুড়ে বিস্তৃত। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যোগী ও সাধু সন্ন্যাসীদের আনাগোনা ছিল বলে এ স্থানটির নামকরণ ‘যোগীর ভবন’ হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়।
এখানে রয়েছে একটি আশ্রম, চারটি মন্দির, কানচ কূপ, একটি ইদারা, ধর্মটুঙ্গি ও অগ্নিকুণ্ড ঘর। সমগ্র বসতিস্থল বা ভবনসমূহের এলাকা প্রাচীর বেষ্টিত এবং একটি বিভাজক দেয়াল দ্বারা দুভাগে বিভক্ত। পশ্চিমভাগে ধর্মটুঙ্গি ও গদিঘর নামক দুটি মন্দির রয়েছে। পূর্ব ভাগে রয়েছে সর্বমঙ্গলা, দুর্গা, কালভৈরবী ও গোরক্ষনাথসহ ৪টি মন্দির।
স্থাপত্যশৈলী ও লিপি প্রমাণে অনুমান করা হয়, যোগীর ভবনস্থ মন্দিরগুলো সতেরো-আঠারো শতকে নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ এসব মন্দিরের নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে, কিংবদন্তির বেহুলার মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দর এখানকার কানচ কূপের পানির মাধ্যমে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।
এসব উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ছাড়াও দেখতে পারেন মানকালীর ধাপ, বৈরাগীর ভিটা, খোদার পাথর ঢিবি, জিয়ৎ কুণ্ড, গোবিন্দ ভিটা, গোকুল মেধ, কানাই বিহার, গোদাই বাড়ির ধাপ, সন্যাসীর ধাপ, স্কন্ধের ধাপ, ওঝা ধন্বন্তরির ভিটা, জাহাজ ঘাটা, তাম্র দুয়ার, বাবুর পুকুর গণকবর, প্রেম যমুনার ঘাট, সৌদিয়া সিটি পার্ক, পর্যটন মোটেল।
ভ্রমণের প্রস্তুতি:
পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও ছোট কিছু ভুল আপনার আনন্দময় ভ্রমণকে বিব্রতকর করে তুলতে পারে। তাই ভ্রমণকে আরো উপভোগ্য এবং স্মরণীয় করে তুলতে কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন। ভ্রমণের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারেন।
লিস্ট তৈরি করা
ভ্রমণের সময় আপনি কী কী করবেন এই পরিকল্পনাগুলো লিখে ফেলুন। এতে করে আপনার ভ্রমণের সময় যথাযথ ব্যবহার করা যাবে। লিস্ট অনুযায়ী ঠিক করুন কোথায় কোথায় যাবেন এবং সেখানে কত সময় অতিবাহিত করবেন।
হালকা লাগেজ
লাগেজ যতটা সম্ভব হালকা রাখার চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় জিনিস এড়িয়ে চলুন। তাহলে আপনি খুব সহজেই ব্যাগ বহন করতে পারবেন। অন্যথায় ভারী ব্যাগ আপনার ভ্রমণকে তিক্ত করে তুলতে পারে।
সঠিকভাবে প্যাকিং
স্যান্ডেল বা জুতা পলিথিন বা কাগজে মুড়িয়ে ব্যাগে নিন এতে কাপড় ও অন্যান্য জিনিস পত্র নোংরা হবে না। এ জাতীয় ছোট ছোট বিষয়ে খেয়াল রাখুন।
স্থানীয় খাবার
ভ্রমণে যতটুকু সম্ভব স্থানীয় খাবার খাবেন এবং সেই খাবারের স্বাদ বুঝতে চেষ্টা করবেন। আপনি যদি ঘুরতে গিয়ে নিয়মিত রেস্টুরেন্টে খাবার খান তাহলে আপনার ঘুরতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তাই ট্যুরিস্ট রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে স্থানীয় লোকজন যেখানে খায় সেখানে খাবার চেষ্টা করুন।
অফ-সিজন ভ্রমণ
ভ্রমণ মৌসুমের বাইরে ভ্রমণ করলে খরচ কমে আসবে। অফ সিজনে সাধারণত পর্যটক কম থাকে। তাই হোটেল থেকে শুরু করে পরিবহন ও খাবার প্রায় সব জায়গাতেই আপনি কম খরচে চলতে পারবেন। তাই অফ সিজনে ভ্রমণ পরিকল্পনা করুন।
যাতায়াতের ব্যবস্থা
ভ্রমণের স্থানের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে নিন। কারণ এসব ভ্রমণে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঠকতে হয় স্থানীয় যানবাহন ভাড়া নিয়ে। ভাড়া সম্পর্কে ধারণা না থাকলে গাড়িচালকরা আপনার থেকে অতিরিক্ত ভাড়া চাইবেন।
অতিরিক্ত টাকা
ভ্রমণে সবসময় আপনার বাজেটের বাইরে কিছু টাকা সাথে রাখুন। যেকোনো সময় যেকোনো বিপদে এই অতিরিক্ত টাকা আপনাকে হেল্প করবে। আপনি চাইলে মোবাইল ব্যাংকিং বা ডেবিট ক্রেডিট কারডের মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত টাকা সাথে রাখতে পারেন।
ছোট ব্যাগ
ভ্রমণে মোবাইল, মানিব্যাগ ও ছোট ছোট দরকারি জিনিসপত্র রাখার জন্য ছোট একটি ব্যাগ সঙ্গে রাখুন। কিছু ব্যাগ পাওয়া যায় যেটি কোমরে রাখা যায়।
চার্জার
মোবাইল ও ল্যাপটপের চার্জার নিতে ভুলবেন না। পাওয়ার ব্যাংক হলে সবচেয়ে ভালো হয়। রুমের বাইরে যাবার সময় পাওয়ার ব্যাংকটি সঙ্গে নিতে পারেন। ছবি তোলার ক্ষেত্রে মোবাইলের চার্জ অনেক বেশি খরচ হয়। তাই পাওয়ার ব্যাংক সঙ্গে রাখা নিরাপদ।
ইয়ারফোন
ভ্রমণের সময় কাটানোর জন্য ইয়ারফোন বা এমপিথ্রি প্লেয়ার সঙ্গে নিতে পারেন। ছোট মাপের কোনো স্পিকার সঙ্গে নিতে পারেন। এতে করে গ্রুপের সবাই একসঙ্গে গান শুনতে পারবেন এবং একটি ভালো আড্ডা জমে উঠবে।
ঢাকা থেকে যেভাবে যাবেন:
ঢাকার গাবতলী বা মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে সরাসরি বাসে এবং কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ও বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে বগুড়া শহর যেতে পারেন।
বাস: ঢাকা থেকে বগুড়া রুটের নন এসি বাস ভাড়া হলো সর্বনিম্ন ৫৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫০ টাকা এবং ঢাকা টু বগুড়া রুটের এসি বাসের ভাড়া ১,১০০ (সর্বনিম্ন) থেকে ১,৩০০ টাকা (সর্বোচ্চ)। ঢাকা থেকে বগুড়া রুটে নিয়মিত যেসকল বাস যাতায়াত করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— আনিতা এন্টারপ্রাইজ, এসআই ট্রাভেলস, আহাদ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস, রাব্বানী পরিবহন, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, একতা ট্রান্সপোর্ট, এস আর ট্রাভেলস ইত্যাদি। সহজ ডট কমের মাধ্যমে অনলাইনে পেয়ে যাবেন বিভিন্ন বাসের টিকিট। টিকিট কাটতে এখানে ক্লিক করুন। এছাড়া বাসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে গিয়েও টিকিট কাটতে পারেন।
ট্রেন: ট্রেনে গেলে যেতে পারেন আন্তনগর রংপুর এক্সপ্রেস বা লালমনি এক্সপ্রেসে। ট্রেনের টিকিট কাটতে এখানে ক্লিক করুন।
যেখানে থাকবেন:
মম ইন পার্ক এন্ড রিসোর্ট
ঠিকানা: নওদাপাড়া, রংপুর রোড, বগুড়া
মোবাইল: ০১৭৫৫-৬৬৯৯০০
ওয়েবসাইট: momoinn.com
হোটেল নাজ গার্ডেন
ঠিকানা: বগুড়া সিটি বাইপাস, সিলিমপুর, বগুড়া – ৫৮০০
মোবাইল: ০১৭৫৫-৬৬১১৯৯
ওয়েবসাইট: hotelnazgarden.com
হোটেল লা ভিলা
কর্পোরেট অফিস ঠিকানা: বাড়ি-৩৩, রোড-৫, ব্লক-এফ, বনশ্রী, ঢাকা, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭৭৪-৯৭৪৮৪৯
ওয়েবসাইট: hotellavilla.j-alisongroup.com
যা খাবেন:
বগুড়ায় আকবরিয়া বা শ্যামলী হোটেলে খেতে পারেন। এ ছাড়াও আকবরিয়ার দই, এশিয়ার দই ও মিষ্টি, চিনিপাতার দই ও চুন্নুর গরুর চাপ খেতে পারেন।
সতর্কতা:
ইট-পাথরের শহরের কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে ভ্রমণের জন্য আকুল থাকে মন। তবে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে ভ্রমণ হয়ে উঠবে আরো আনন্দময়। ভ্রমণে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে—
পরিকল্পিত ভ্রমণ
পরিকল্পিতভাবে ভ্রমণ করলে যাত্রা আরামদায়ক ও নিরাপদ হয়। যদি বাস বা ট্রেনের টিকিট বুকিং করার সুযোগ থাকে, তাহলে মাঝামাঝি আসন নিন। রাতের বেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে জানালার পাশে বা বাসের খুব পেছনের আসন এড়িয়ে চলাই ভালো।
নির্ভরযোগ্য যানবাহন ব্যবহার
নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য বাস বা যানবাহন বেছে নিন। সরকারি বা স্বীকৃত পরিবহন সংস্থার যানবাহন ব্যবহার করুন। বাস বা গাড়ির রুট ও সময়সূচি সম্পর্কে আগেই জেনে নিন। অ্যাপ-ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং পরিষেবা (যেমন উবার, পাঠাও) ব্যবহার করলে গাড়ির তথ্য যাচাই করুন।
ভিড় এড়িয়ে চলুন
খুব বেশি ভিড় থাকলে বা সন্দেহজনক পরিস্থিতি দেখলে সেই যানবাহনে না ওঠাই ভালো। গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র যেমন মানিব্যাগ, ফোন বা ব্যাগ নিজের কাছেই রাখুন।
জরুরি নম্বর সংরক্ষণ করুন
স্থানীয় পুলিশ, বাস সার্ভিস হেল্পলাইন ও পরিচিতজনের নম্বর সহজেই পাওয়া যায় এমন জায়গায় রাখুন। বিপদের সময় ৯৯৯ (বাংলাদেশের জরুরি সেবা) তে কল করুন।
যাত্রাপথে অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া কিছু খাবেন না
যাত্রাকালে অনেক যাত্রী পার্শ্ববর্তী যাত্রীকে ভদ্রতার খাতিরে বা বন্ধুসুলভভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণে অনুরোধ করেন। এ ধরণের পরিস্থিতিতে ঝুঁকি এড়াতে অপরিচিত ব্যক্তির দেয়া কিছু না খাওয়া নিরাপদ।
মোবাইল ফোন নিরাপদে রাখুন
অনেকেই বাসে বা গণপরিবহনে যাত্রাকালে মোবাইল ফোন বের করে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং করেন। এ ধরনের অভ্যাস ছিনতাইয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে জানালার পাশে বসলে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোন বের না করে নিরাপদ। সম্ভব হলে, যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফোন বের না করে, নিরাপদে পকেটে বা ব্যাগে রাখুন।