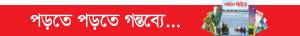অনেকদিন আগের ঘটনা তো সন তারিখ সঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের আগস্টের শেষদিকে, বাংলা ভাদ্রের প্রথমদিকে হবে। কী কারণে যেন স্কুল /কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিনের ছুটি ছিল। তখন হঠাৎ বাবুল বলল- ‘তোমার কুষ্টিয়া তথা শিলাইদহ যাবার ব্যবস্থা করে এলাম। তবে বিশেষ কারণে আমি তোমার সাথে যেতে পারছি না। তুমি যাবে হাসনা (আসল নাম নয়) ফুফুর সাথে।’ মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। এমন একটি চমৎকার ও আকর্ষণীয় প্রস্তাবে সম্মতি না দেয়ার প্রশ্নই আসে না। এখানে হাসনা ফুফুর একটু পরিচয় দিই। আপনারা নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন, বন্ধুর ফুফু যখন নিশ্চয় কোনো মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা হবেন। আরে না, আমার বন্ধুর ফুফু আমার বন্ধুর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট, টিন-এজ, ইডেন কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। দীর্ঘাঙ্গী অতি আকর্ষণীয় ফিগার ও চেহারার অধিকারিনী। আমার বন্ধু বাবুল তার দাদার প্রথম পক্ষের বড় ছেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর হাসনা ফুফু হচ্ছেন তার দাদার দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে, অর্থাৎ বাবুলের বাবার সৎবোন। কাজেই বাবুলের ফুফু- আমাদের সকলের ‘হাসনা ফুফু’। শিলাইদহ দেখার পরম সৌভাগ্য, আর উপরি পাওনা এমন ভ্রমণসঙ্গী (সঙ্গিনী), এরকম সুযোগ হেলায় হারানোর মতো বোকা আমি ছিলাম না। তখনকার দিনে ছেলে মেয়েদের আজকালকার মতো এমন অবাধ মেলামেশার অবস্থা ছিল না। (আমার বয়স তখন ২২/২৩, ফুপুর বয়স ১৮/১৯ বছর) কোনো তরুণী মেয়ের সাথে কোনো অনাত্মীয় তরুণের একলা কোথাও যাওয়া তো একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে বন্ধুবরের ছিল আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস।
পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পরদিন সকাল ৯টায় আমি ফুলবাড়িয়া রেল ষ্টেশনে (পুরোনো স্টেশনে) হাজির হই। দেখি, হাসনা ফুফু প্ল্যাটফরম আলোকিত করে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কি রংয়ের শাড়ি পরে ছিল, তা এতদিন পর আর মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, তাকে ওই শাড়িতে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। টিকিট কিনে অপেক্ষমান ট্রেনে উঠে বসি। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ে। ট্রেন চলতে থাকলে ফুফুর গা ঘেঁষে একটু ঘনিষ্ট হয়ে বসার চেষ্টা করি, সহযাত্রীদের চোখকে বাঁচিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলি ধরে নড়াচড়ার চেষ্টা করি। কিন্তু না, ফুফু আমার দিকে বাঁকা চেখে চেয়ে একটু করে মিষ্টি হেসে সরে বসে এবং আমার হাতটা সরিয়ে দেয়। তার এই হাসি ও তার প্রসাধনের গন্ধ (না শরীরের গন্ধ, জানি না) আমার সারা দেহে কাঁপন তোলে। সুডৌল বাহুলতা ও বঙ্কিম দেহবল্লরী অবলোকন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে সারাক্ষণ ঘনিষ্ট হয়ে বসার ও গোপনে একটু হাত ধরার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।
দুপুরের দিকে আমরা কুষ্টিয়া পৌঁছে যাই। তারপর ট্রেন বদল করে লোকাল ট্রেনে চড়ি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কুমারখালী পৌঁছি। গ্রামের মাঝে স্টেশন, লোকজনের ভিড় নেই। স্টেশনের বাইরে এসে ফুফু তার গ্রামের বাড়িতে যাবার জন্য একটি এক্কা ভাড়া করে। এক্কা হলো ছই দেওয়া গরুর গাড়ির মতো, আকারে একটু ছোট, এক ঘোড়ায় টানে। এরকম গাড়িতে আমি আগে আর কোনোদিন চড়িনি। গাড়িতে উঠে আমি আর ফুফু সামনাসামনি বসি। মনে হলো আমার সামনে ‘মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’। এবারো খেবরো কাঁচা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। পথের শোভা অপূর্ব। পথের দুধারে ছবির মতো গ্রাম, গ্রামের মধ্যে খড়ের চালের মাটির ঘর। ঘরের সামনে বা পাশে ছোট ছোট ক্ষেতের মাচায় ঝুলে আছে শশা বা করলা বা লাউ। রাস্তার পাশে কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বা সবজি ফলে আছে। তবে পথের এই অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো পূর্ণ অবকাশ ছিল না। অসমতল উঁচু নিচু রাস্তার কারণে প্রবল ঝাঁকুনিতে একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে নতুবা একবার সামনে, একবার পেছনে কাত হয়ে পড়ছি। গাড়ির কাঠের/বাঁশের ফ্রেমে ধাক্কা খেয়ে মনে হচ্ছিল হাড়গোড় বুঝি ভেঙে না যায়। বোধ হয়, সঠিকভাবে বসতে না জানার কারণেই আমার অবস্থা কাহিল। অথচ আমার সামনে ফুফু দিব্যি বসে এই দুলুনি উপভোগ করছে। তবে সান্তনা এই যে, তীব্র ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝে সহযাত্রিনীর গায়ের ওপর পড়ছি। তার দেহের স্পর্শ ও উষ্ণতা আমার সকল কষ্টকে মুছে দেয়। আর মনে হলো তখন ফুফু তার গায়ে পড়াকে যেন একটু প্রশ্রয়ই দিচ্ছিল। ভাবছিলাম, এ পথ যদি শেষ না হয়। কিন্তু না, সেই সৌভাগ্য হয় না, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ফুফুর বাড়ি পৌঁছে যাই।
‘বাড়ির তরুণী মেয়ে অনাত্মীয়, অপরিচিত ও ভিন্ন ধর্মের এক যুবককে একা ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে’- এই ব্যাপারটি গ্রামের বাড়ির লোকজন কিভাবে নেবে, তা নিয়ে আমার একটু শঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখলাম ফুপু পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর সবাই আমাকে পরম আদরে গ্রহণ করে। একে একে বাড়ির সবার সাথে পরিচিত হই। বাবুলের দাদা অর্থাৎ ফুফুর আব্বা আমার থাকা খাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাপড়চোপড় বদলিয়ে চা নাস্তা খেয়ে ফুফুর ছোট ভাই ও ভাতিজার সাথে বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে আসি। পুকুরটি বেশ বড় এবং পাড়ে রয়েছে বড় বড় গাছ, ভারি সুন্দর। পুকুরের তিনদিকে নিচু জমিতে ধানক্ষেত, কাঁচাপাকা আউশ ধানে পরিপূর্ণ। ধানক্ষেতে নাকি বড় বড় কই মাছ পাওয়া যায় এবং ছোট ছোট ছিপ দিয়ে তা ধরা যায়। আমরা পুকুর পাড়ে শান বাঁধানো ঘাটে বসি। কিছুক্ষণ পর ফুফুর আব্বাসহ আরও কয়েকজন এসে যোগ দেন। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বসে গল্পগুজব করি।
রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শোবার জন্য হাসনা ফুফু আমাকে ডেকে দোতলার একটি রুমে নিয়ে যায়। আমার বিছানা ঠিক করে মশারি টাঙায়। আশে পাশে কেউ নেই। আমি পেছন দিক থেকে তাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরি। তারপর আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে তার কমলার কোয়ার মতো স্ফুরিত ওষ্ঠে আমার ঠোঁট চেপে ধরি। ফুফু এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, উষ্ণ নরম পেলব দুটি উচ্চ পর্বত আমার বুকে লাগে। আমার ওষ্ঠ দুটি ফুফুর ঠোঁট থেকে সরিয়ে গÐাদেশে আনি। শরীরে দুলুনিতে আবৃত বক্ষদেশ কিছুটা অনাবৃত হলে, তখন দেখি অর্ধন্মোচিত বক্ষদেশে সুডৌল স্তনযুগল। আমি আর একটু ঘনিষ্ট হতে চাইলে বলল- ‘আজ এ পর্যন্তই থাক’। এই বলে নিজেকে বিযুক্ত করে নেয়। আমাকে আর দুষ্টুমি না করে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। তারপর প্রাণ-হননকারী কটাক্ষ হেনে, কোমর/নিতম্ব দুলিয়ে দেহবল্লরীতে লাস্যময় ভঙ্গিমা তুলে দরজা ভেজিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। আমি বিছানায় বসে শরাহত বিহঙ্গের মতো ভেজানো দরজার দিকে চেয়ে থাকি। এরপর কি আর নিদ্রা আসে, না এ অবস্থায় কেউ কোনোদিন ঘুমুতে পেরেছে?
পরদিন সকালে চা-নাস্তা করে শিলাইদহের উদ্দেশে বের হই। আমার গাইড হিসাবে দেয়া হল সেই দুজনকেই, একজন হাসনা ফুফুর ছোট ভাই, আর একজন ভাতিজা। বাহন সেই এক্কা গাড়ি। এবরো খেবরো ঊঁচু নিচু রাস্তায় টক্কর খেতে খেতে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সামনে হাজির হই। গাড়ি থেকে নেমে কুঠিবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আবেগ উচ্ছ¡াস ও নস্টালজিয়ায় শিহরিত হই।
কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোরশেদপুর গ্রামে কুঠিবাড়ি অবস্থিত। এক সময় বৃটিশদের নীলকুঠিও ছিল শিলাইদহে। কবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুর ১৮৩০ সালে তৎকালীন বৃহত্তর রাজশাহী জেলার পতিসর ও পাবনার শাহজাদপুরের জমিদারির মালিক হন। এই সকল জমিদারির কেন্দ্রস্থল ছিল শিলাইদহ। তাই এখানেই ৩০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় এই কাছারি বাড়ি। প্যাগোডাধর্মী স্থাপত্যশৈলীর তিনতলা চোখ জুড়ানো মন ভুলানো অপরূপ এই কুঠিবাড়ি। দক্ষিণমুখী এই বাড়ির চারিদিকের বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে পদ্মার ঢেউয়ের আদলে। জমিদারির কাজ তদারকির জন্য এখানে কবির পিতা এবং ঠাকুর পরিবারের অন্য সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে শিলাইদহে এসেছেন। মুগ্ধ হয়েছেন কুষ্টিয়ার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে। কবিগুরু প্রথমবার শিলাইদহ এসেছিলেন অন্যদের সাথে ১৮৭৬ সালে। ১৮৯২ সালে শিলাইদহ জমিদারির ভার গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে এসে থাকেন। ১৮৯২ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শিলাইদহে ছিলেন বা যাওয়-আসা করতেন।
তিনতলা ভবনটির প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় ৮টি করে ১৬টি এবং তৃতীয় তলায় ২টি, মোট ১৮টি কক্ষ রয়েছে। তৃতীয় তলায় ছিল কবির লেখার ঘর। উত্তরে পদ্মা ও দক্ষিণে গড়াই এই দুই নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে বসে তিনি রচনা করেছিলেন তার অনেক বিখ্যাত গান, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ১৬টি কক্ষে রবীন্দ্রনাথের নানা রূপের ও নানা বয়সের ছবি ও তার ব্যবহার্য আসবাবপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। তৃতীয় তলায় আছে তার ব্যবহৃত আসবাবপত্র, তার হাতের লেখা কবিতা ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সনদপত্রের কপি। কবির ব্যবহৃত জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে- কাঠের চেয়ার, টি-টেবিল, সোফা সেট, আরাম কেদারা, হাত পালকি, শোয়ার পালংক, চীনামাটির ওয়াটার ফিল্টারসহ আরও নানা জিনিস। কবির নিজের আঁকা বেশ কয়েকটি চিত্রকর্মও রয়েছে। তবে সবচেয়ে দৃষ্টি কাড়ে ৮ ও ১৬ বেহারার পালকি এবং চঞ্চলা ও চপলা নামে দুটি স্পিডবোট।

মূল ভবনের পাশে বিখ্যাত দুই বিঘা জমির আম্রকানন। মনে হলে দূরের বড় আমগাছটির গোড়ায় বসে আছে দুই বিঘা জমির সেই উপেন। কুঠিবাড়ির পশ্চিমে বিখ্যাত পুকুর বা দিঘি। শান বাঁধানো ঘাটের দুপাশে দুটি বকুল বৃক্ষ, যা কবিগুরুর নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন। পুকুরের ঘাটলায় বসে কবি কত অবসর সময় কাটিয়েছেন, দেখেছেন- ‘স্তব্ধ অতল, দিঘি কালো জল…’। আমিও বেশ কিছুক্ষণ পুকুরের ঘাটে বসে প্রশান্ত পরিবেশ উপভোগ করি।
শিলাইদহে অবস্থানকালে কবিগুরু পদ্মায় বহু ভ্রমণ করেছেন। ভাসমান বোটে পদ্মাবক্ষে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, পদ্মা/গড়াইয়ের অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। পদ্মাবক্ষে বসে লিখেছেন নানা গদ্য-পদ্য। এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের কথা তার রচনায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
পরবর্তীকালে আমি জীবনের বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত বহু স্থানে গিয়েছি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেছিলেন বা যে সকল স্থান তার পদচারণায় ধন্য হয়েছিল, যেমন বাংলাদেশে পতিসর, শাহজাদপুর, শ্বশুরবাড়ি ফুলবাড়িয়া, ভারতে জোড়াসাঁকো, দার্জিলিং, কালিম্পং, মংপু, কার্সিয়াং, রাঁচি ও আগরতলা এবং সুদূর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এবং সবশেষে শান্তি নিকেতনে। কিন্তু জীবনের প্রথম দেখা রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ আমার হৃদয়মনে অন্যরকম স্থান দখল করে আছে।
দুপুর দেড়টার দিকে আমরা ফুফুর বাড়িতে ফিরে আসি। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে পুকুর পাড়ে আসি। ফুফুর ভাই-ভাতিজা ছিপ নিয়ে আসে মাছ ধরার জন্য। আমিও ওদের সাথে একটি ছিপ নিয়ে ধানক্ষেতের ধারে বসে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও দুটি কই মাছ ধরে ফেলি। সাঁঝের অন্ধকার নেমে এলে আমরা উঠে আসি।
সন্ধ্যার পর সবাই মিলে অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও আড্ডার পর রাতের খাবার খাই। খাবারে আমাদের ধরা মাছ ছাড়াও ছিল আরও বহু আয়োজন। খাওয়ার পর শুতে গেলে আগের রাতের নাট্যাংশটি প্রায় হুবহু পুনারাভিনয় হয়। ঘটনাপর্ব ‘আজ এই পর্যন্তই থাক’-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো, পরবর্তীকালেও তা আর অতিক্রম করা হয়নি, ওই পর্যন্তই থেকে গেছে। তবে স্মৃতিটুক কোনোদিন অমলিন হয়নি।
পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমি ঢাকায় ফিরে যাবার জন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিই। ট্রেন ধরার জন্য আগের দিন ঠিক করে রাখা ঘোড়ার গাড়িতে কুমারখালী রওনা হই। ফুফুর ক্লাস বন্ধ, তাই ফুফু বাড়িতে থাকবে, আমার সাথে যাচ্ছে না, এবার আমার একা নিসঙ্গ নিরানন্দ যাত্রা। একদিকে শিলাইদহ দেখার অনেকদিনের আকাক্সক্ষা পূর্ণ হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে আরও কি যেন হতে পারত কিন্তু হয়নি, সেই অতৃপ্তির গোপন বেদনা নিয়ে ঢাকায় ফিরে চলেছি। মনকে শান্তনা দিই, যা পেয়েছি তাও বা কমকী।
লেখক: প্রকৌশলী জেবি বড়ুয়া