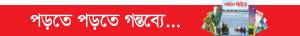১০ মে, ২০২২। সুইডেনের স্টকহোমের আরলান্ডা এয়ারপোর্ট থেকে আনুষ্ঠানিকতা সেরে বের হতে অনেকখানি সময় লাগলো। দাপ্তরিক কাজে সুইডেন এসেছি। টিমের অন্যদের থেকে আমি আলাদা, ফ্লাইটের ভিন্নতার কারণে। দেখা হবে চার-পাঁচ ঘণ্টা ট্রেন দূরত্বে কালমার শহরে। কালমার পর্যন্ত পৌঁছানোর তিনটা ট্রেন টিকিট আয়োজকরা আমাকে আগেই পাঠিয়েছে। প্রথমে এয়ারপোর্ট থেকে স্টকহোম সেন্ট্রালের ট্রেন খুঁজে বের করলাম পুলিশের সহায়তায়। কিন্তু টিকিটে লেখা সময় অনুযায়ী এখনো ট্রেনের সময় হয়নি। একটু সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। মহিলা পুলিশ কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো, ‘এটাই স্টকহোম সেন্ট্রালের ট্রেন। উঠে পড়ো’।
উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ল। ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমের নির্ধারিত সময় ১৮ মিনিট। সামনের মনিটরে ট্রেনের গতি দেখা যাচ্ছে। ১৭০, ৮০, ৯০, মাঝে মধ্যে ২০০ পেরিয়ে যাচ্ছে। আয়েশি ভ্রমণ উপভোগ করছি। এর মধ্যেই আয়েশ ভঙ্গকারী টিকিট চেকারের আগমন! টিকিটের বদলে সবাই মোবাইল ফোন এগিয়ে দিচ্ছে। আমি প্রিন্ট করা কাগজটা এগিয়ে দিলাম। ভ্রু কুঁচকালো চেকার। আমার টিকিট পছন্দ হয়নি! আমি নাকি লোকাল ট্রেনের টিকিট নিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠেছি। আমার কী দোষ? আমি তো পুলিশকে জিজ্ঞেস করেই ট্রেনে উঠেছি।
‘তাহলে বাড়তি ভাড়া নিয়ে নাও’, আমি বললাম।
‘হবে না,’ চেকার বললো। ‘এটা অন্য কোম্পানির ট্রেন। গন্তব্যে গিয়ে পুরো ভাড়া দিয়ে নতুন টিকিট কিনতে হবে।’
তাই হলো। সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে চেকার আমাকে টিকিট কাউন্টারে নিয়ে গেলো এবং বেশ কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে আবার টিকিট কিনলাম।
কালমারের পথে আমার পরবর্তী গন্তব্য আলভেস্তা জংশন। ওখানে গিয়ে আবার ট্রেন বদল করতে হবে। টিকিট চেকার আমাকে বুঝিয়ে দিলো কোন প্লাটফর্মে যেতে হবে। ১০ নম্বর প্লাটফর্ম খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। টিকিটের তথ্য অনুযায়ী যে ট্রেনে উঠলাম, এটির গন্তব্য কোপেনহেগেন। আমাকে মাঝপথে নেমে পড়তে হবে। সামনে বসা সহযাত্রীকে টিকিট দেখিয়ে নিশ্চিত হলাম আমি আর ভুলের চক্রে নেই। আলভেস্তায় ট্রানজিট মাত্র ১২ মিনিটের। সহযাত্রী আশ্বস্ত করলেন- সমস্যা হবে না। উনিও কালমার যাবেন। ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড নিয়ে ট্রেনে বসেই দেশে কথা বললাম, যদিও গন্তব্যে পৌঁছাইনি এখনো। মনে পড়লো ১৯৮০ সালে লিবিয়ায় পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পর দেশ থেকে প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম।
নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট পর ট্রেন আলভেস্তায় থামলো। পাশের প্লাটফর্মে দাঁড়ানো কালমারের ট্রেনে উঠে বসলাম। সহযাত্রী এবার অন্য কামরায়। এবারের ভ্রমণ স্বল্প সময়ের। কালমারে ট্রেন থামলো শেষ বিকালে। ট্রেন থেকে নেমে আশপাশে তাকালাম। গতকাল ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি। রাত কেটেছে দুবাই এয়ারপোর্টে। আজ সারাদিন আকাশে আর রেলপথে। কোনো চেনা মুখ দেখিনি। সুইডিশ সহকর্মী আনা মারিস এগিয়ে এসে আমার সুটকেস হাতে নিলো। ভিনদেশে, অচেনা জনপদে এই চেনা বিদেশিনিকে এই মুহূর্তে অনেক আপন মনে হলো। আনার বন্ধুর গাড়িতে হোটেলে পৌঁছালাম। ক্লান্ত শরীরে একটু থিতু হওয়ার সুযোগ পেলাম।
আমাদের প্রতিষ্ঠান এমআরডিআই থেকে একটা বড়সড় দল সুইডেনে এসেছি, সাথে কয়েকজন সাংবাদিকও রয়েছেন। তবে সবার অংশগ্রহণ এক রকম নয়। আমরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ও কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছি।
কালমার একটা নিরিবিলি, ছিমছাম ও সুন্দর শহর। এখানকার লিনিয়াস ইউনিভার্সিটির ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট আমাদের প্রোজেক্ট পার্টনার। সে সুবাদেই আমাদের এই সফর। কালমারে আমরা পুরো দুদিন থেকেছি। ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট আর কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভিজিট করেছি। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য- প্রাচীনতম দৈনিক ইধৎড়সবঃবৎহ কার্যালয় পরিদর্শন। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত সুইডিশ ভাষার এই পত্রিকাটি এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও ডিজিটাল বিকাশ, মহামারি, মিডিয়া জগতে পরিবর্তনের ধারা- এসব কারণে পত্রিকা ব্যবস্থাপনা, পাঠকের সংখ্যা ও ধরনে উত্থান-পতন হয়েছে। সম্পাদক ও অন্যদের সাথে বৈঠক শেষে পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখলাম। মনে পড়লো ৪৩ বছর আগে ১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে দিল্লিতে ঞরসবং ড়ভ ওহফরধ পত্রিকার অফিস পরিদর্শন করেছিলাম। পত্রিকা অফিসের চেহারা একেবারেই ভিন্ন। টেলিপ্রিন্টার, কম্পোজ রুম, এডিটিং, পেজ মেকআপ টেবিলের জায়গা দখল করে নিয়েছে শুধুই কম্পিউটার। প্রযুক্তির উন্নয়ন পরিবর্তন এনেছে মানুষের চিন্তায়, আচরণে।
কালমারের পর আমাদের গন্তব্য আনার বাড়ি। একটা মাইক্রোবাসে আমরা পাঁচজন আর সুইডিশ সহকর্মী মারিয়াকে নিয়ে আনা নিজেই ড্রাইভ করে রওনা হলো। পথে একটা সুপার মার্কেটে সবাই কিছু কেনাকাটা করলো। আমি কিনলাম একটা বেল্ট। কারণ দুবাই এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেকের পর বেল্টটা ওখানে ফেলে এসেছি। আরেক জায়গায় থেমে আনার মেয়ে আর ওর বান্ধবীকে উঠিয়ে নিলাম।
অজ পাড়া গাঁ বলতে যা বোঝায়, আনার বাড়ি তেমনই এক জায়গায়। শান্ত, সুবোধ বাল্টিক সাগরের পাড়ে সুন্দর দ্বিতল বাড়ি। আজ আমাদের খাওয়া আর আলসেমি করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। বাড়িটার চারপাশ খোলা। এটা কোনো সাজানো গ্রাম নয়। একটু দূরে দূরে বাড়ি। যেদিকে সাগর ওই পাশটাতে একটা খোলা চত্বর। বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে। বাড়ি আর সাগরের মাঝখানে কিছু ঝোপঝাড়। সাগরের পাড়ঘেঁষে কাঠের চমৎকার ওয়াকওয়ে। আমি, দোলন আর আনা হাঁটতে বের হলাম। পাড়ে ছোট-বড় বেশ কিছু বোট নোঙর করা। এর মাঝে ছোট একটি বোট আনার। মেয়েকে নিয়ে মাঝে মাঝে রোয়িং করে। আনা আমাদের জন্য খাওয়াদাওয়ার অনেক আয়োজন করেছে। দুপুর আর রাতের (বিকালে) খাবার সেরে আমরা ভ্যাকো (ঠধপধীঁ) নামে ছোট একটা শহরে গেলাম। এখানকার হোটেলেই আজ রাত যাপন। ফুলের শহর ভ্যাকো। ইউরোপে এরকম অনেক শহর আছে বলে শুনেছি। দেখা হয়েছে খুব কমই। ১৯৮৩ সালে নবপরিণীতাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এরকম এক সুন্দর শহরে। প্যারিস থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে সেই ছোট্ট শহর ভিশি।
এখানে আমাদের অবস্থান স্বল্প সময়ের। দাপ্তরিক কোনো কাজ নেই। সকালে নাশতার পর আমি, সেলিম আর দোলন হাঁটতে বের হলাম। রাস্তায় মানুষজন খুব কম। ব্যস্ত ঢাকা শহর থেকে এসে ব্যাপারটা একটু অস্বস্তির। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে থামলাম। বাড়ির ছাদে একটা টিভি এন্টেনা লাগানো। যে প্রযুক্তিকে আমরা ২০ বছর আগেই বিদায় জানিয়েছি। সুইডেনের তো দেশে ব্যাপারটা বিস্ময়েরই!
ভ্যাকো থেকে ট্রেনে স্টকহোম পৌঁছালাম বিকালে। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে হেঁটে হোটেলে গেলাম। এই জায়গাটা একটু বিভ্রান্তিকর। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে হোটেল লবিতে এসে চাবি নিয়ে লিফটে এক ধাপ নেমে রুমে গেলাম। রুমের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি- খোলা আকাশের নিচে রেললাইন, ট্রেন। ভূমি উচ্চতার এই বিষয়টি আমার কাছে রহস্য হয়েই রইলো।
স্টকহোমে তিনদিন আমাদের বেশ ব্যস্ততায় কাটলো। এর মাঝে রয়েছে আইটিপি কনফারেন্সের উদ্বোধন, ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট স্টকহোম অফিসে কয়েকটি মিটিং, কয়েকটি পত্রিকা ও টিভি স্টেশন পরিদর্শন। আইটিপি কনফারেন্সে আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হাসিবুর রহমান, সহকর্মী লাবণ্য আর চেনা অচেনা কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে দেখা হলো। পরদিন শহরতলির দিকে একটি কমিউনিটি পত্রিকা অফিসে গেলাম। নির্ধারিত সংখ্যক পত্রিকা তালিকাভুক্ত পাঠকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পাঠকের কাছে খবর পৌঁছানোই লক্ষ্য।
এ পর্যায়ে আমাদের গ্রæপ আবার বিভাজিত হলো। আমি, তানিম, লাবণ্য আর ফোয়োর সহকর্মী মারিয়া- এই চারজন সিডা আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য স্টকহোম থেকে চার ঘণ্টা বিশ মিনিট ট্রেন দূরত্বে হারনোস্যান্ডে হাজির হলাম।
হারনোস্যান্ড একটি প্রায় জনবিরল শহর। কিছুক্ষণ পর পর রাস্তায় একটা গাড়ি দেখা যায়। তবে সবাই শৃঙ্খলা মেনে চলে শতভাগ। গাড়ি থাকুক বা না থাকুক, লাল সিগন্যালে অবশ্যই থেমে থাকবে, সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত। রাস্তার পাশে একটু উঁচু সাইকেল লেন, আরেকটু উঁচুতে ফুটপাত। অনভ্যস্ত আমি সাইকেল লেন দিয়ে হাঁটছিলাম। মারিয়া আমার ভুল ধরিয়ে দিলো।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি পরিবেশ অনুক‚ল। নাশতায় ডিম ছাড়া আর কোনো খাবারে প্রাণিজ আমিষ নেই। পুরো কেন্দ্রটি সৌর বিদ্যুতে পরিচালিত। খোলামেলা অবস্থানে বিদ্যুতের ব্যবহারও কম। কেন্দ্রের পাশেই একটা জলাশয়। গাছপালা, ফুল, পাখি- কোনো কিছুরই কমতি নেই। বিচিত্র সব গাঙচিল, কবুতরের ওড়াউড়ি, জলাশয়ে হাঁস আর মাছরাঙার দাপাদাপি। ট্রেন ভ্রমণের সময়ও প্রচুর জলাশয় দেখেছি। আনাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সুইডেনে এরকম এক হাজার লেক আছে। গ্রিন এনার্জি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে উইন্ডমিল আর সোলার প্যানেল। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বৈশ্বিক অঙ্গীকারের প্রতি সুইডেন শ্রদ্ধাশীল ও যতœবান।
তিনদিনের কর্মশালায় ছিল একটি আনন্দময় শিখন পরিবেশ। এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণকারী ক্লাসরুম সেশন, গ্রæপ ওয়ার্ক আর গেমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন।
হারনোস্যান্ড থেকে আবার ভাগ হয়ে তানিম আর মারিয়া চলে গেলো উত্তর সীমান্তে লুলিয়া শহরে, আমি আর লাবণ্য স্টকহোমে। আবার ভাগ হয়ে লাবণ্য চলে গেলো ওর টিমে যোগ দিতে, আমি আমার হোটেলে। আবার একা হয়ে গেলাম।
আগামী দুদিন তেমন ব্যস্ততা নেই, ফোয়ো অফিসে একটা মিটিং ছাড়া। একটু ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। এখানকার সহকর্মী ক্যাটারিনার সহায়তায় সুযোগটা চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি। স্টকহোম শহরের পুরোনো এলাকা হচ্ছে গামলাস্তান। আজ বিকালে গামলাস্তান ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা। ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসহ কয়েকটি দেশের অংশগ্রহণকারীর একটি দল। বাংলাদেশ থেকে শুধু আমি। ক্যাটারিনা আমাকে বুঝিয়ে বললো- কীভাবে আমি হোটেল থেকে গামলাস্তান পৌঁছাবো। হাঁটতে হাঁটতে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আর ক্যাটারিনার সাথে ফোনে কথা বলে কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছি না। আমার অবস্থানও ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না। ক্যাটারিনা আমাকে বললো, ‘তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আর টেলিফোনটা কাউকে দাও’। আমি একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। কাউন্টারে বসা তরুণী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। হয় তো ভেবেছে আমি একজন ক্লায়েন্ট। টেলিফোনটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘কথা বলো’। একটু অবাক হয়ে সে টেলিফোন হাতে নিলো। সুইডিশ ভাষায় কিছু কথোপকথন হলো। টেলিফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে তরুণী বললো, ‘অপেক্ষা করো’। তিন মিনিটের মধ্যে ক্যাটারিনা চলে এলো। নিরহংকার, সদাহাস্য এই নারী কোনো কিছুতেই বিরক্ত হয় না।
অপ্রশস্ত গলি আর পুরোনো ভবন গামলাস্তানের বৈশিষ্ট্য, যেন ইতিহাস বইয়ের একটি অধ্যায়। সবকিছু পুরোনো হলেও পরিচ্ছন্নতায় কমতি নেই। ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আর ছবি তুললাম। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে যে জায়গাটায় এসে থামলাম, সেটি হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি। অন্যান্য ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার নরওয়ে থেকে দেয়া হলেও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় এই সুইডিশ একাডেমি থেকে। পাশেই পার্লামেন্ট ভবন, একটু উঁচু জায়গায়। অনেক মানুষ এই এলাকায় বেড়াতে এসেছে বিকালে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফোয়ো অফিসে চলে এসেছি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম, আলাপচারিতা। তারপর ডিনার, সূর্য ডোবার আগেই। ক্যাটারিনা আমাকে শহর দেখাতে বের হলো। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে অ্যালকোহল টেস্ট দিলো। একটা পাইপ মুখে নিয়ে ফুঁ দিলো। এই টেস্টে কোয়ালিফাই না করলে গাড়ি স্টার্ট নেবে না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ড্রাইভিংয়ের বিরুদ্ধে এই সতর্কতা।
বড়সড় একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ড্রাইভ করে বিচ এলাকায় একটা পার্কে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। ক্যাটারিনা আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওর মেয়েকে আনতে। আমি ওকে দাওয়াত দিলাম পরদিন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার জন্য।
বলা যায়, আজই সুইডেনে আমার শেষ দিন। আগামীকাল ডেনমার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অন্যরা নানা দলে ভাগ হয়ে গেলেও আমি আলাদা যাচ্ছি ডেনমার্কে ফারুক মামার বাড়ি হয়ে যাবো বলে।
ক্যাটারিনা এলো ১১টার দিকে। সেভেন ইলেভেন থেকে খাবার আনতে গিয়ে জেনেছিলাম, এখানে শান্তি নামে একটা ইন্ডিয়ান চেইন রেস্টুরেন্ট রয়েছে। হোটেলের পেছনের রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে একটু নিচে নেমে নদীর পাড় দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম। চমৎকার জায়গা, চমৎকার পরিবেশ। মানুষজন কেউ হাঁটছে, কেউ জগিং বা সাইক্লিং করছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা ব্রিজ পার হয়ে গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে আমরা যেখানে পৌঁছালাম ওটা শুকরিয়া নামে একটা রেস্টুরেন্ট, শান্তি চেইনের আউটলেট। ভেতরে বসে জানতে পারলাম, মালিকের বাড়ি সিলেট। লন্ডনে যত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, সবগুলোর মালিক বাংলাদেশি। ইউরোপেও তারই ঢেউ। ক্যাটারিনার পছন্দ মতো ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস অর্ডার দিলাম। বাটি ভরা মাংস, কিন্তু একটা কাপে খানিকটা রাইস দিলো, খিচুড়ি হিসেবে যা মানোত্তীর্ণ নয়। অবশ্য ক্যাটারিনা অনেক প্রশংসা করলো খাবারের। প্রশংসা করা নিঃসন্দেহে ওদের একটা চারিত্রিক গুণ। লাঞ্চ শেষে আমরা গেলাম ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। সুইডেনের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন, নিকট অতীতের কিছু প্রযুক্তি উপকরণ যেমন- টেলিফোন সেট, টাইপ মেশিন, অ্যাডিং মেশিন, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ছবি তুললাম।
মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে কাছেই একটা জেটিতে গেলাম। ছোট বড় জাহাজ নোঙর করা। এসব জাহাজে করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে পর্যটকরা। আমার সুইডেন ভ্রমণের এখানেই ইতি। আগামীকাল থেকে ডেনমার্কে সংক্ষিপ্ত সফর।
স্টকহোম এয়ারপোর্ট থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনে চড়ে উড়াল দিলাম, গন্তব্য ডেনমার্কের বিলুন্দ এয়ারপোর্ট। একটু পর এয়ার হোস্টেস এলো একটা স্ন্যাকসের ট্রলি নিয়ে। চা ছাড়া সবকিছু পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। এক প্যাকেট বাদাম, পানি আর চা নিয়ে নগদ টাকা এগিয়ে দিলাম। কিন্তু না। বার পোস্টে লেগে বল ফিরে এলো। নগদ চলবে না। কার্ড দিয়ে পে করতে হবে। ইউরোপে আসার পর থেকেই এই সমস্যায় ভুগছি। কার্ড নেই, বলে বাদাম আর পানি ফিরিয়ে দিলাম। প্রবীণ মানুষটাকে দেখে মেয়েটার বোধ হয় মায়া হলো! একটু হেসে বিনা পয়সায় খাবারগুলো দিয়ে চলে গেলো।
ছোট ছিমছাম এয়ারপোর্ট বিলুন্দ। ১৯৮৩ সালে এর চেয়েও ছোট এয়ারপোর্ট মাল্টায় অবতরণ করেছিলাম নববধূকে নিয়ে। তবে তখনকার মাল্টার চেয়ে এই বিলুন্দ এয়ারপোর্ট অনেক সুন্দর আর গোছানো। প্লেন থেকে নামার পাঁচ- সাত মিনিটের মধ্যে ব্যাগ পেয়ে গেলাম। শেনযেন ভিসা। তাই ইমিগ্রেশন বা কাস্টমসের কোনো বালাই নেই।
বের হয়েই দেখি ফারুক মামা আর মামি (হ্যানে) দাঁড়িয়ে। এই মামিকে আমি বাংলাদেশে দেখেছি কয়েকবার। অত্যন্ত আন্তরিক আর স্নেহময়ী, বাঙালি নারীর মতোই। ফারুক মামা আমার আম্মার মামাতো ভাই, বয়সে আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ না করেই চলে এসেছেন ডেনমার্কে। সেই থেকে জীবিকা, বিয়ে, সংসার, জীবন যাপন এখানেই।
গাড়িতে মামার পাশে আমি বসলাম। মামি পেছনে। কিছু দূর যাওয়ার পর আমি বললাম, ‘ক্যাটারিনা গতকাল আমাকে বলেছে বিলুন্দ এয়ারপোর্টের কাছেই নাকি লেগো ল্যান্ড’। মামা সাথে সাথে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যদিকে রওনা দিলেন। এখনই দেখে যেতে হবে। পরে সময় হবে না। লেগো ল্যান্ডে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। কারণ, এটা মামার প্ল্যানের বাইরে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি, ছবি উঠানো, তারপর আবার রওনা।
একটা বিচে গিয়ে থামলাম। জায়গাটার নাম ‘ভিডি স্যানডে’. একটা উইন্ডমিল টাওয়ার রয়েছে ওখানে। জ্বালানির সবুজায়নে অনেক এগিয়েছে ডেনমার্ক। উইন্ডমিল আর সোলার এনার্জির ব্যবহার দিন দিনই বাড়ছে।
মামি খাবার নিয়ে এসেছেন বক্সে করে। সাথে চাদর, প্লেট, চামচ। প্রচÐ বাতাস। কাশবনের মতো একটা জায়গায় চাদর বিছিয়ে লাঞ্চ করলাম। খাবারে মামির যতেœর ছোঁয়া।
ডেনমার্কে আমার তিনদিনের ঘোরাফেরা মামার পরিকল্পনা মতো। প্রথম দিন অবস্থান বিংঃ নধু-তে মামার সামার রিসোর্টে। জঙ্গলের মতো একটা জায়গায় একটা ঘর। একটু দূরে দূরে আরও কিছু ঘর। গাড়ি বাইরেই রাখা হয়। রাতের খাবার হলো একেবারে মনের মতো- পরোটা, গরুর মাংস, ভাত। রান্না ও গেরস্থালি কাজে মামা খুবই পারদর্শী। পরদিন থর্স মিনে নামক একটা জায়গায় মাছের আড়ত দেখতে গেলাম। শেড দেয়া বড় একটা জায়গা। মাছ কেনাবেচা, প্রসেসিং, প্যাকেজিং সব কিছুরই ব্যবস্থা এখানে। পাশেই বাল্টিক সাগর। পাথুরে সৈকত ধরে হাঁটাহাঁটি করলাম।
পরবর্তী গন্তব্য মামার শহরের বাড়ি সিল্কেবোর্গ। শহরের কোলাহল অবশ্য এখানে নেই। নিরিবিলি সুন্দর একতলা বাড়ি, আধুনিক সব সুযোগ সুবিধাসহ। বাড়ির পেছনে একটু জঙ্গল, দু-তিনটা হরিণের আবাস। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে। খরগোশের আনাগোনাও রয়েছে। বাড়ির সামনে সুন্দর লন। স্মার্ট একটা ঘাস কাটার (সড়বিৎ) যন্ত্র আছে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে লনের ঘাস ছেঁটে দেয় এই যন্ত্রটি। কবে, কখন, কতটুকু ছাঁটতে হবে- সব প্রোগ্রাম করে দেয়া আছে। কোনো ম্যানুয়াল বা রিমোট কন্ট্রোলের দরকার পড়ে না। সময় শেষে ওর নির্ধারিত ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাড়িতে কেউ না থাকলেও সে তার দায়িত্ব পালন করে।
সিল্কেবোর্গে দুদিন অবস্থানের সময় কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি। এখানে চমৎকার একটি ঝরনা ধারা আর একটি পার্ক রয়েছে। এক জায়গায় একটি কাঠের টেবিলের মতো- ওতে সাত সুর টিউন করা। পাশে স্টিক রাখা আছে। টেবিলে আঘাত করলে সা রে গা মা সুর বেজে ওঠে। এক কোণায় রয়েছে শিশুদের একটি প্লেগ্রাউন্ড।
বাঙালির মামা বাড়ির আবদার অনেকটা অধিকার বলেই বিবেচিত হয়। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কদিন মামা-মামির কাছ থেকে যে আদর আপ্যায়ন পেয়েছি, এক কথায় তা অসাধারণ। আমি নিশ্চিত, বাঙালি মামি হলেও এর চেয়ে বেশি আন্তরিকতা পেতাম না। আমি আপ্লুত হয়েছি সেদিন, যেদিন দেখলাম- মামি নিজ হাতে বেক করা বিস্কুট একটা বক্সের সাথে প্যাক করে দিলেন আমার পরিবারের জন্য। আমি নতুন করে উপলব্ধি করলাম, ভালোবাসা কোনো মানচিত্র, সীমান্ত, জাতীয়তা, সংস্কৃতির বিভেদ মানে না। ভালোবাসার শক্তি অপরিসীম।
সিল্কেবোর্গ থেকে কোপেনহেগেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টার ড্রাইভ। আমাকে বাসে বা ট্রেনে উঠিয়ে না দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেয়াটাই ছিল মামার পরিকল্পনায়। আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে মামা-মামি যাবেন ছেলের বাড়িতে। ফ্লাইট যদিও সন্ধ্যায়, আমরা সকাল সকাল রওনা দিলাম। মাঝে এক জায়গায় থামলাম। খাবার নিয়ে সাগর পাড়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। দামাল বাতাস আমার হ্যাট উড়িয়ে নিলো। মাথায় চুল সংকটের কারণে দেশেও শীতের দিনে ক্যাপ বা হ্যাট পরতে হয়। আর এখানে তো এটা আরও প্রাসঙ্গিক। সাগরে পড়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে হ্যাট কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।
এখান থেকে একটি ১৮ কিলোমিটার লম্বা সেতু পাড়ি দিলাম। এটি হচ্ছে জিলেন্দে-ফুনেন সেতু, ডেনমার্কের দুই অংশকে যুক্ত করেছে। এক সময় এটা ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু। এর রেল অংশটুকু মাঝামাঝি গিয়ে সাগরের নিচে ঢুকে পড়েছে। ওপারে গিয়ে ডাঙায় উঠেছে।
কোপেনহেগেন এয়ারপোর্টে পৌঁছেও মামা আমাকে একা ছাড়লেন না। গাড়ি পার্ক করে চেক-ইন পর্যন্ত আমার সাথে রইলেন। যেন আমি গ্রাম থেকে ঢাকায় বেড়াতে আসা আত্মীয়! মামা-মামিকে বিদায় জানিয়ে ডিপার্চার লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। দুবাই হয়ে দেশে ফিরবো। অনেক দিন পর একটু লম্বা সময় বিদেশে কাটালাম। দেশে ফেরার খুশি অনুভব করতে শুরু করেছি। ইনহাস্ত ওয়াতানাম।
মো. সাহিদ হোসেন
লেখক: